ইতিহাসের ধারণা ৷ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস (প্রথম অধ্যায়) Concept of history ৷ Class 7 history 1St chapter.
১. ইতিহাস বর্ণনা করার সময় কোন বিষয়গুলির ওপর আপাতভাবে জোর দেওয়া হয়?
উত্তর: ইতিহাস বর্ণনা করার সময় স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আপাতভাবে জোর দেওয়া হয়।
২. একটি নদীমাতৃক সভ্যতার নাম করো।
উত্তর: সিন্ধু সভ্যতা হল একটি নদীমাতৃক সভ্যতা।
৩. ভারতবর্ষের নামটি কোন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে হয়েছে?
উত্তর: ভারতবর্ষের নামটি ‘ভরত’ জনগোষ্ঠীর নামানুসারে হয়েছে।
৪. ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ভাগ করেছে কোন পর্বত?
উত্তর: বিন্ধ্য পর্বত ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ভাগ করেছে।
৫. দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের সীমানা বিন্ধ্য পর্বত থেকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?
উত্তর: দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের সীমানা বিন্ধ্য পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত।
৬. যে-কোনো একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন-এর নাম লেখো।
উত্তর: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।
৭. হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যখন বরফ জমেছিল, তখন তাকে কী বলা হত?
উত্তর: হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যখন বরফ জমেছিল, তখন তাকে বলা হত তুষার যুগ।
৮. প্রাক্-ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: প্রাক্-ইতিহাস বলতে বোঝায় ইতিহাসের আগের সময় অর্থাৎ, যখন মানুষ লিখতে জানত না।
৯. কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?
উত্তর: কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক।
১০. হর্ষাব্দ গণনা কত খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়?
উত্তর: খ্রিস্টাব্দ থেকে হর্ষাব্দ গণনা শুরু হয়।
১১. কার জন্মসাল থেকে খ্রিস্টাব্দ গণনা চালু হয়?
উত্তর: জিশুখ্রিস্টের জন্মসাল থেকে খ্রিস্টাব্দ গণনা চালু হয়।
১২. কবে থেকে গুপ্তাব্দ গণনা শুরু হয়?
উত্তর: ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গুপ্তাব্দ গণনা শুরু হয়।
১৩. খ্রিস্টাব্দ গোনা হয় কীভাবে?
উত্তর: ছোটো থেকে বড়ো হিসাবে খ্রিস্টাব্দ গোনা হয়।
১৪. ‘প্রশস্তি’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘প্রশস্তি’ শব্দের অর্থ হল গুণগান করা।
১৫. খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: জিশুখ্রিস্টের জন্মের আগের সময়কালকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে।
১৬. প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ কী?
উত্তর: প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ হল ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার জন্য বিরাট এলাকা জুড়ে খননকাজ চালানো এবং প্রাপ্ত উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্যসংগ্রহ করা।
১৭. প্রত্নক্ষেত্র বলতে কী বোঝো?
উত্তর: প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রত্নবস্তু পাওয়ার জন্য যে অঞ্চলে খননকাজ চালান সেই অঞ্চলকে প্রত্নক্ষেত্র বলে।
১৮. কোথায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যত্ন করে রাখা থাকে?
উত্তর: জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যত্ন করে রাখা থাকে।
১৯. ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম হল ঋগ্বেদ।
২০. প্রাচীন ভারতের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের নাম লেখো।
উত্তর: প্রাচীন ভারতের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের নাম হল অষ্টাধ্যায়ী।
২১. শক-কুষাণদের ইতিহাস কোথা থেকে জানা যায়?
উত্তর: শক-কুষাণদের ইতিহাস জানা যায় মুদ্রা থেকে।
২২. হর্ষচরিত বইটি কে লেখেন?
উত্তর: হর্ষচরিত বইটি লেখেন বাণভট্ট।
২৩. বাণভট্টের হর্ষচরিত কী ধরনের গ্রন্থ?
উত্তর: বাণভট্টের হর্ষচরিত জীবনীমূলক গ্রন্থ।
২৪. নদীমাতৃক সভ্যতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: প্রাচীনকালে মানুষ নদীর ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। তারা নদীর জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করে নদী উপত্যকাগুলিতে চাষবাস শুরু করে। সেখানে তারা পশুপালনও শুরু করে। ক্রমে কৃষিকে কেন্দ্র করে ওইসব স্থানে এক একটি মানব সভ্যতা (যেমন-সিন্ধু সভ্যতা) গড়ে ওঠে। যেহেতু সভ্যতাগুলি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেজন্য এই ধরনের সভ্যতাকে বলা হয় নদীমাতৃক সভ্যতা।
২৫. সমতল অঞ্চলের লোকেরা খাদ্য হিসেবে ভাত গ্রহণ করে কেন?
উত্তর: সমতল অঞ্চলে নানা কারণে ধান চাষ বেশি হয়। এর ফলে এই অঞ্চলের লোকেরা ভাত প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।
২৬. আর্যাবর্ত বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: আর্যদের বাসস্থান এক জায়গায় স্থির ছিল না, নানা সময়ে পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় তারা ভারতে বসবাস করত। ভারতের উত্তর অংশে যেখানে আর্যরা বসবাস করত সেই অঞ্চলকে আর্যাবর্ত বলা হত।
২৭. কোন অঞ্চলকে দ্রাবিড় দেশ বলা হত?
উত্তর: দ্রাবিড়রা বসবাস করত ভারতের দক্ষিণ দিকে। এই দক্ষিণ 1 দিককে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। কাবেরী নদীর দক্ষিণ অংশকে তাই দ্রাবিড় দেশ বলা হত।
২৮. তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ কাকে বলে?
উত্তর: যে-যুগে মানুষ তামা ও বোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন পাত্র, যন্ত্রপাতি, অলংকার ও হাতিয়ার ব্যবহার করত। সেই যুগকে বলা হয় তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ।
২৯. প্রায়-ইতিহাস যুগ কাকে বলে?
উত্তর: যে-সময়ে মানুষ লিখতে শিখেছিল এবং যে-সময়ের অনেক লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। সেই সময়কে প্রায়-ইতিহাস যুগ বলা হয়।
৩০. ইতিহাস কাকে বলে?
উত্তর: মানুষের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা ও সভ্যতার পরিবর্তন এবং উত্থান-পতনের ধারাবাহিক বিবরণকে ইতিহাস বলে।
৩১. সময়ের হিসাব কীভাবে করা যায়?
উত্তর: সাল-তারিখ, বছর-অব্দ প্রভৃতি দিয়ে সময়ের হিসাব করা হয়।
৩২. খ্রিস্টাব্দ কাকে বলে?
উত্তর: জিশুখ্রিস্টের জন্মকে ধরে যে-অব্দ বা সাল গণনা করা হয় তাকে খ্রিস্টাব্দ (AD = Anno Domini) বলা হয়।
৩৩. শতাব্দ ও সহস্রাব্দ কী?
উত্তর: একশো বছরকে শতাব্দ বা শতাব্দী এবং হাজার বছরকে একসঙ্গে সহস্রাব্দ বলা হয়।
৩৪. প্রত্নতাত্ত্বিক কাদের বলে?
উত্তর: দীর্ঘদিন ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা পুরোনো দিনের উপাদানগুলিকে যাঁরা খননকার্য চালিয়ে খুঁজে বের করেন এবং ইতিহাস রচনার কাজে সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেন তাঁদের প্রত্নতাত্ত্বিক বলে।
৩৫. ইতিহাসের উপাদান কাকে বলে?
উত্তর: প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া মানুষের ব্যবহার করা নানা জিনিস, মুদ্রা, গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, মূর্তি প্রভৃতি ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করে। এগুলিকেই ইতিহাসের উপাদান বলে।
৩৬. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কাকে বলে?
উত্তর: বহুকাল ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা উপাদান (যেমন-মানুষের দেহাবশেষ, ব্যবহৃত সামগ্রী প্রভৃতি) যেগুলি ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলে।
৩৭. শিলালেখ কাকে বলে?
উত্তর: পুরোনো দিনের যে-সকল লেখাগুলি পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে, সেই লেখাগুলিকে শিলালেখ বলে। যেমন-অশোকের শিলালেখ।
৩৮. মুদ্রা কীভাবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে?
উত্তর: মুদ্রা থেকে রাজার নাম, বংশ পরিচয়, মূর্তি, রাজ্যসীমা, রাজত্বকাল, ধর্মবিশ্বাস, শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ, রাজ্যের উন্নতি, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রভৃতি কথা জানা যায়। এই সকল তথ্য ইতিহাস রচনাকালে আমাদের সাহায্য করে।
৩৯. সাহিত্যিক উপাদান বলতে কী বোঝো?
উত্তর: সাহিত্যিক উপাদান বলতে লিখিত উপাদানকে বোঝায়। যেমন-রামায়ন, মহাভারত।
৪০. ইতিহাসের উপাদান বলতে কী বোঝানো হয় ?
উত্তর: পুরোনো দিনের বহু জিনিস যা আজও রয়ে গেছে সেগুলি আমাদের অতীতের কথা জানতে সাহায্য করে। প্রাচীন। ঘর-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ, মূর্তি, টাকাপয়সা, ছবি ও বইপত্র থেকে আমরা এক-একটা সময়কালের মানুষের বিষয়ে জানতে পারি। তাই এইগুলিই হল ইতিহাসের উপাদান।
৪১. ইতিহাস পড়ার দরকার হয় কেন?
উত্তর: এমন অনেক ঘটনা এবং কাজ আগে ঘটেছে কিন্তু তার ছাপ আজও আমাদের চারপাশে রয়ে গেছে, সেই ঘটনা এবং কাজগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। সেই ধারণা তৈরি করার জন্যই ইতিহাস পড়া দরকার।
৪২. ইতিহাসে কেন সাধারণ মানুষ বা শিল্পীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না?
উত্তর: সে সময় শিল্প বা সাহিত্য সবেতেই সাধারণ গরিব মানুষের কথা খুব বেশি থাকত না। তাতে বেশিরভাগই ছিল শাসকের গুণগানে ভরা। তাই সাধারণ কারিগর এবং শিল্পী যারা মন্দির বা স্থাপত্য বানিয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগের নামই আমরা ইতিহাসে পাই না।
৪৩. ইতিহাস বইতে সামান্য হলেও সাল-তারিখ থাকে কেন?
উত্তর: যেসব ঘটনার কথা ইতিহাস বইতে থাকে, সেগুলো আজ থেকে অনেক বছর আগে ঘটেছিল এবং সেগুলো একই দিনে বা একই বছরে ঘটেনি। তাই প্রকৃত সময়কালকে জানতে হলে ঠিক মতো করে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নিতে হয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন ঘটনাগুলোর সময়কাল। তাই সাল-তারিখগুলি যতই জটিল হোক, পাছে আমরা সময়ের হিসেবে গোলমাল করে ফেলি তাই ওগুলি মনে রাখতে হবে। তাই ইতিহাস বইতে অল্প হলেও সাল-তারিখ থাকবেই।
৪৩. ঐতিহাসিক জটিল নামগুলি নিয়ে কেন দুশ্চিন্তা থেকে যায়?
উত্তর: ঐতিহাসিক অনেক নাম বা উপাধি খুবই গোলমেলে, মনে রাখা খুবই কঠিন। যেমন—’গঙ্গাইকোল্ড চোল’ বা ‘সকলোত্তরপথনাথ’। কিন্তু এই উপাধিগুলি অনেককাল আগের মানুষদের। তারাও হয়তো এতো বড়ো নাম-উপাধি নিয়ে গোলমালে পড়তেন। কিন্তু ওই সময় এমনই বড়ো শক্ত উপাধি ও নামের চল ছিল। তাই এগুলো তো আর এখন বদলে নেবার উপায় নেই বা ছোটো করে নেওয়াও সম্ভব নয়।
৪৪. ইতিহাসের উপাদানগুলি নানা ভাগে বিভক্ত কেন?
উত্তর: ইতিহাসের সব উপাদান একরকম নয়। একটা পুরানো মূর্তি, পুরানো মুদ্রা বা পুরানো বই এক জিনিস নয়। তাই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লিখিত উপাদান। পাথর বা ধাতুর পাতে লেখা থেকে পুরোনো দিনের অনেক কথা জানা যায়, সেগুলোকে বলে লেখ। তামার পাতে লেখাগুলিকে বলা হয় তাম্রলেখ, পাথরের উপর লেখাগুলিকে বলে শিলালেখ এবং কাগজের লেখাগুলিকে বলা হয় লিখিত উপাদান।
৪৫. ইতিহাসে আদি-মধ্যযুগ বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর: হঠাৎ করে বা রাতারাতি ইতিহাসের যুগ বদলে যায় না। যেমন দুপুরবেলা বলতে কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সময়কে বোঝায় না। কারণ সময়টা কিন্তু না সকাল না বিকেল। তেমনই ভারতের ইতিহাসে একটা বড়ো সময় ছিল, যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগও পুরোপুরি শুরু হয়নি। ঐতিহাসিকরা সেই সময়টাকে বলেন আদি-মধ্যযুগ।
৪৬. বিদেশি ও দেশ এর বর্তমান অর্থ কী ?
উত্তর: বর্তমানে আমরা বিদেশি বলতে ভিন্ন দেশের বাসিন্দাকে বুঝি। আমাদের দেশ ভারত, তাই ভারত ছাড়া অন্য যে-কোনো দেশের লোককে আমরা বিদেশি বলে মনে করি।
৪৭. সুলতানি বা মুঘল যুগে ‘বিদেশি’ বলতে কী বোঝানো হত?
উত্তর: সাধারণ অর্থে ‘বিদেশি’ বলতে আমরা ভারতের বাইরের বা অন্য দেশের লোকেদের বুঝি। কিন্তু সুলতানি বা মুঘল যুগে ‘বিদেশি’ বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে-কোনো লোককেই বোঝাতো। তাই শহর থেকে অচেনা কেউ গ্রামে গেলে তাকেও গ্রামবাসীরা ‘পরদেশি’ বা ‘আজনবি’ ভাবতেন। তাই ইতিহাস পড়ার সময় আমাদের একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে মুঘল যুগের কোনো লেখায় যদি ‘পরদেশি’ কথাটা ব্যবহৃত হয় তবে সবসময় তা ভারতের বাইরে থেকে আসা কোনো লোককে বোঝাতো না, সে অন্য শহর বা অন্য গ্রামের লোকেদেরও বোঝানো হত। তাই ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিকদের মাথায় রাখতে হয় যে সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে কথার মানে বদলে যায় । ইতিহাস পড়বার সময়েও আমাদের এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে।
৪৮. ইন্ডিয়া’ নামটি কীভাবে এসেছে?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ‘ইন্ডিয়া’ নামটি প্রথম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছিলেন। তিনি পারসিক ভাষায় লেখা পত্র থেকে ভারত সম্পর্কে জেনেছিলেন। যদিও তিনি ভারতে আসেননি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকা কিছুদিনের জন্যে পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন পারসিকরা এই অঞ্চলের নামকরণ করে হিদুষ’। ইরানি ভাষায় ‘স-এর উচ্চারণ নেই, তাই ‘স’-এর বদলে গিয়ে হয়েছিল ‘হ’। ফলে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলগুলি ‘হিদুষ’ নামে পরিচিত হলো। আবার গ্রিক বর্ণমালায় ‘হ’-এর উচ্চারণ নেই। তার বিকল্প হল ‘ই’। অতএব আগে যা ছিল সিন্ধু-হিদুষ, তা গ্রিক ঐতিহাসিকের বিবরণে অনেকটাই বদলে গিয়ে ইন্ডিয়া’ হলো। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেইসময় ইন্ডিয়া শব্দটি সিন্ধু ব-দ্বীপ এলাকাকেই সাধারণ অর্থে বোঝানো হতো। পরবর্তীকালে গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণী পড়লে বোঝা যায় তখন তারা ইন্ডিয়া বলতে উপমহাদেশকেই বোঝাতো।
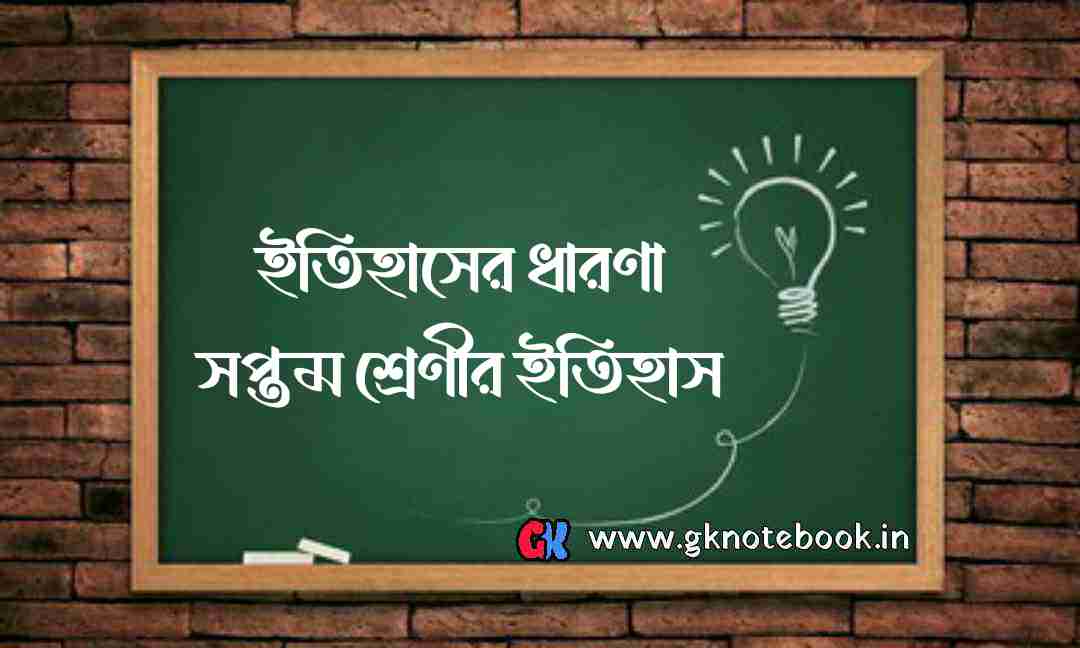
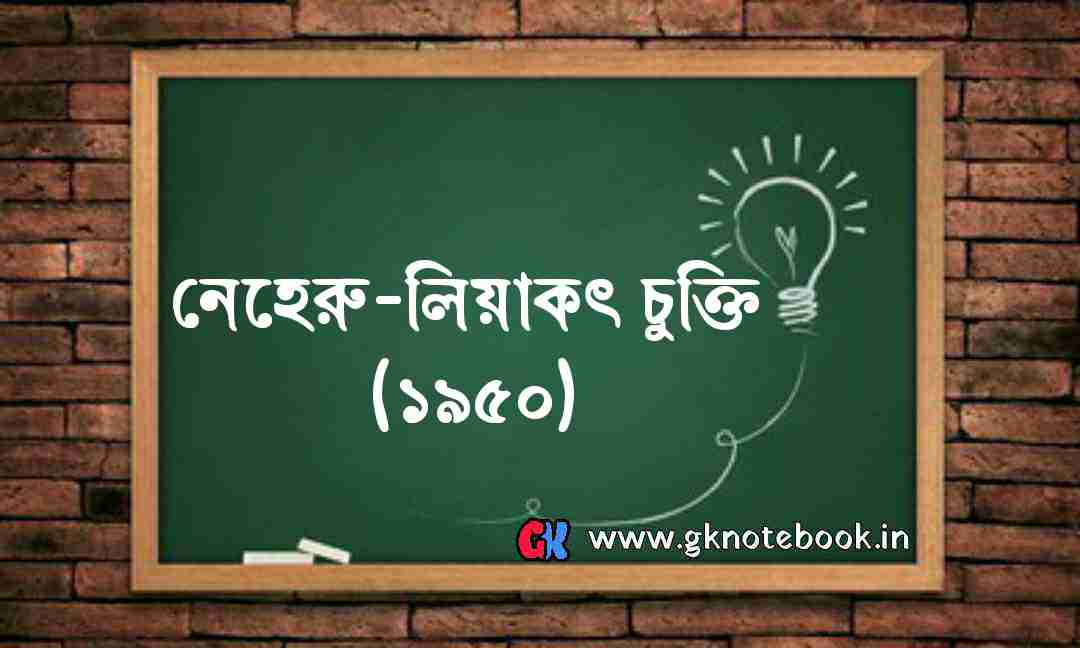
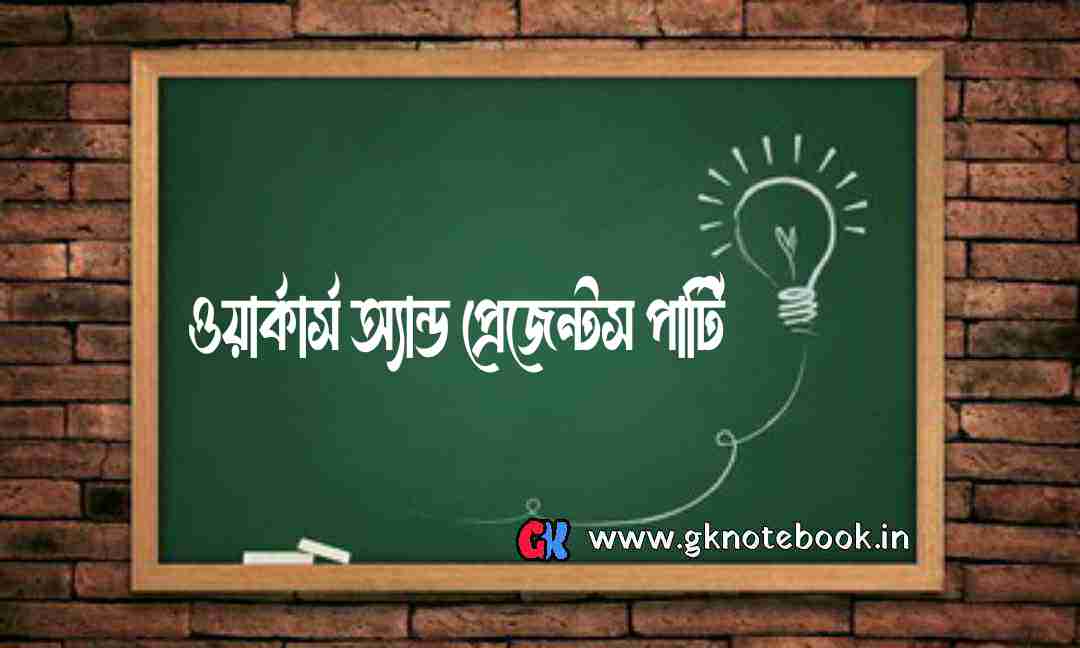
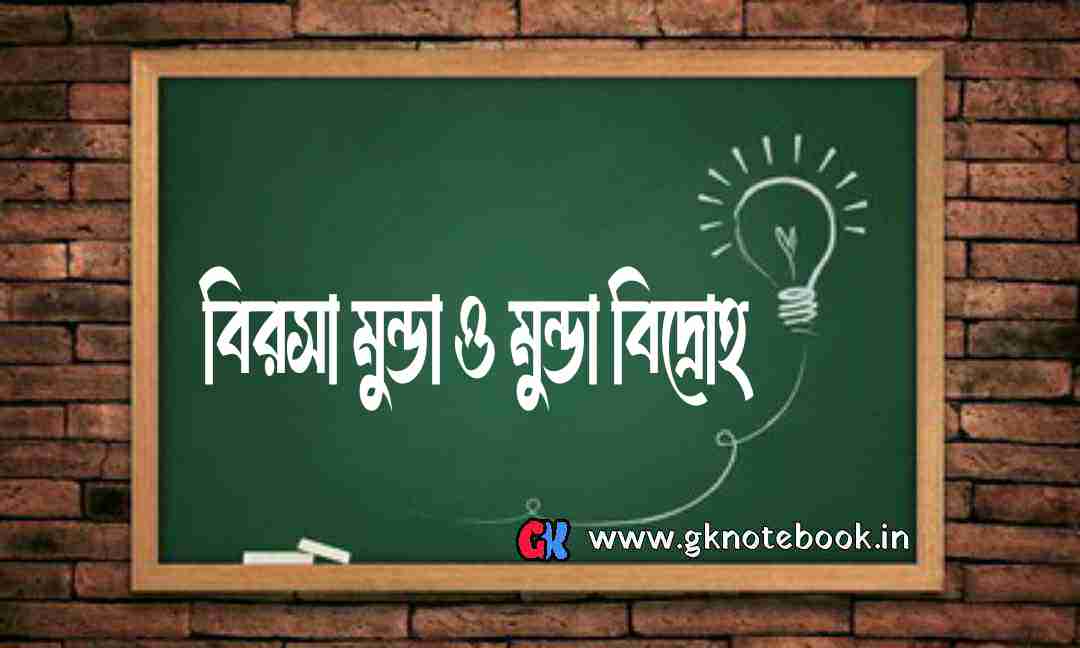
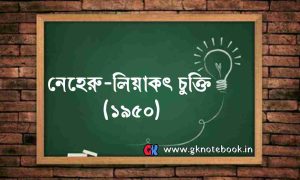
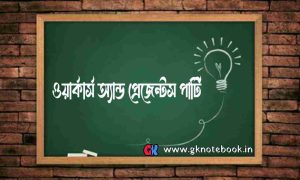
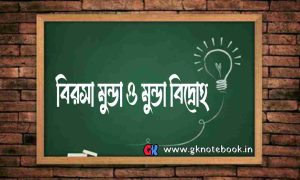

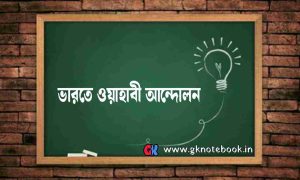
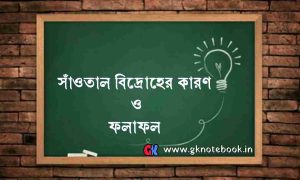
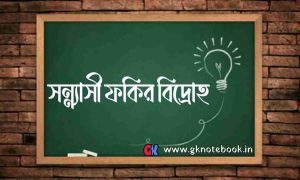
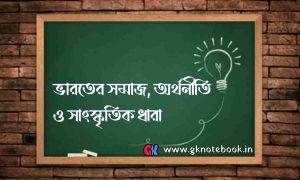
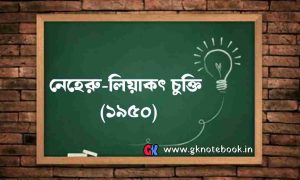
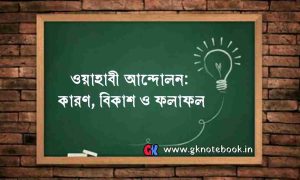
Post Comment