সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল: The Santal Rebellion.
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কালে ভারতে যে সমস্ত কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। কঠোর পরিশ্রমী শান্তিপ্রিয় ও সরল প্রকৃতির কৃষিজীবী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাঁওতালরা ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশদের আশ্রয়পুষ্ট জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তা ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ‘ নামে পরিচিত।
সাঁওতালদের পূর্বকথা:
ভারতের আদিবাসী জনজাতিগুলোর মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী হলো অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী। ডালটন সাহেবের মতে, সাঁওতালরা বীরভূম অঞ্চলে আসে পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে। তারা এসেছিল মূলত চাষবাস ও শিকারের উদ্দেশ্যে। হিন্দু অগ্রগতির চাপে তাদের সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরে আসতে হয়। সাঁওতালরা মূলত বৃহৎ দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর একটি উপজাতি এবং ভাষাগত দিক থেকে ‘কোলারিয়ান’ শ্রেণির।
দামিন-ই-কোহর ইতিবৃত্ত:
দামিন-ই-কোহ’ শব্দটি ফারসি, যার অর্থ ‘পর্বতের পাদদেশ’। এই অঞ্চল বর্তমান সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত।
১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বীরভূম রাজাদের অত্যাচারে সাঁওতালরা বীরভূম ত্যাগ করে গোদ্দা মহকুমা অঞ্চলের বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বসবাস শুরু করে। ১৮৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ৪২৭টি সাঁওতালি গ্রাম সেখানে গড়ে ওঠে।
লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮২৮–১৮৩৫) সরকারিভাবে রাজমহলের পশ্চিমদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে সাঁওতালদের বসবাসের অনুমতি দেন। ফলে ১৮৫১ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে সাঁওতালদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮৩ হাজারে।
কিন্তু ইংরেজ সরকার ক্রমশ রাজস্ব বৃদ্ধি করে এবং জমিদার-মহাজনদের সহযোগিতায় সাঁওতালদের ওপর অমানবিক শোষণ শুরু হয়।
মহাজনরা ৫০% থেকে ৫০০% পর্যন্ত সুদে ঋণ দিত, ফলে সাঁওতালরা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ত। ঋণ শোধ করতে না পারলে তাদের শস্য, গবাদি পশু, এমনকি পরিবার-সহ নিজেকেও বিকিয়ে দিতে হতো।
১৮৪৮ সালে মহাজনদের অত্যাচারে দামিন-ই-কোহের কয়েকটি গ্রামের সাঁওতাল পরিবার দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে নারায়ণ মুর্মুর দুই পুত্র, সিধু ও কানু, সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।
সাঁওতালদের সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৮৫৫–১৮৫৬):
অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসন, জমিদার ও মহাজনদের শোষণে অতিষ্ঠ সাঁওতাল জনগণ যখন জীবনধারণে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তখন সিধু ও কানু মুর্মু নেতৃত্বে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উদ্দেশ্য ছিল—অন্যায় শাসন উৎখাত করে স্বাধীন “সাঁওতাল রাজ” প্রতিষ্ঠা।
বিদ্রোহের সূচনা:
ভগনাডিহ গ্রামে এক সভায় সিধু ও কানু ঘোষণা করেন যে ঠাকুর জিউ স্বপ্নে তাদের বিদ্রোহের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বলেন—ঈশ্বর তাদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও মুক্তির আহ্বান সাঁওতাল সমাজে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।
১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন সিধু-কানুর নেতৃত্বে প্রায় ৪০–৫০ জন সশস্ত্র সাঁওতাল যুবক বিদ্রোহ শুরু করে। পথে তারা দারোগা মহেশ দত্ত ও মহাজন কানু মানিক রায়কে হত্যা করে। এরপরই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভাগলপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মুঙ্গের অঞ্চলে।
সরকারি প্রতিক্রিয়া ও দমন:
১৮৫৫ সালের ১৭ আগস্ট সরকার বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়, কিন্তু সাঁওতালরা তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর ইংরেজ সেনা কামান ও বন্দুক নিয়ে দমন অভিযান শুরু করে। তীর-ধনুকধারী সাঁওতালরা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করলেও ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে টিকতে পারেনি।
ভগনাডিহ গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়, সিধু ও কানুর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কানু মুর্মু অবশেষে ধরা পড়ে এবং ১৮৫৬ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিদ্রোহে প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারায়।
যদিও বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল, তবুও এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎ জনজাতীয় সশস্ত্র আন্দোলন। এই বিদ্রোহ ভারতীয় সমাজে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বসূরি হয়ে ওঠে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ (১৮৫৫–১৮৫৬):
সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসন ও দেশীয় মহাজন-জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে এক বিশাল আদিবাসী আন্দোলন। এর পেছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় নানা কারণ কাজ করেছিল।
রাজস্বের অতিরিক্ত চাপ:
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাঁওতালদের কৃষিজমি কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার আওতায় আসে। জমিদার ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে — যা ‘দামিন-ই-কোহ’ নামে পরিচিত। কিন্তু সরকার সেখানে জমিদারি ব্যবস্থা চালু করায় তাদের উপর আবারও করের চাপ পড়ে, ফলে তারা ক্ষুব্ধ হয়।
মহাজনি শোষণ:
সাঁওতালদের নগদ অর্থে কর দিতে হতো। এজন্য তারা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত। কিন্তু মহাজনরা অতি সুদে টাকা ধার দিত এবং প্রতারণার মাধ্যমে তাদের জমি, গবাদি পশু এমনকি পরিবার পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করত। এই ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্তির জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
ব্যবসায়ীদের শোষণ:
ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে ফসল কম দামে কিনে বেশি দামে জিনিস বিক্রি করত। তারা ‘কেনারাম-বেচারাম’ নামের বাটখারা ব্যবহার করে ওজনেও ঠকাত। এর ফলে বণিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্ম নেয়।
নীলকর সাহেবদের অত্যাচার:
নীলচাষ বাধ্যতামূলক করার জন্য ইংরেজ নীলকররা সাঁওতালদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। নীলচাষে অস্বীকার করলে তাদের সম্পত্তি ও পরিবার লুণ্ঠিত হতো। তাই সাঁওতালরা এর প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নেয়।
সরকারি কর্মচারীদের অবিচার:
সরকারি কর্মচারীরা জমিদার ও মহাজনদের পক্ষ নিয়েছিল। সাঁওতালদের অভিযোগ শোনা হতো না। বরং প্রশাসন তাদের ওপর অন্যায়ভাবে দমননীতি প্রয়োগ করত। ফলে তারা সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ হয়।
রেলকর্মচারীদের অত্যাচার:
লর্ড ডালহৌসির সময়ে রেলপথ নির্মাণের সময় ঠিকাদার ও কর্মচারীরা সাঁওতালদের জোরপূর্বক শ্রমে নিযুক্ত করে নামমাত্র মজুরি দিত এবং তাদের নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর নির্যাতন চালাত। এই সব ঘটনাও বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালে।
ধর্মীয় উন্মাদনা ও নেতৃত্ব:
খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরের চেষ্টায় সাঁওতালদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সিধু ও কানু মুর্মু ঘোষণা করেন যে, ঠাকুর জিউ তাদের বিদ্রোহের নির্দেশ দিয়েছেন।
তারা প্রচার করেন—“ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন।”
এই বিশ্বাস ও ধর্মীয় উন্মাদনা তাদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে।
অবশেষে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভাগনাডিহিতে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে ১০ হাজার সাঁওতাল সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসার:
- ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন ভাগনাডিহি গ্রাম থেকে সিধু ও কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিদ্রোহ ভাগলপুর, মুঙ্গের, বীরভূম, রাজমহল, দেউগড় ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।
- বিদ্রোহী সাঁওতালদের সঙ্গে কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর প্রভৃতি নিম্নবর্গের হিন্দু কারিগর সম্প্রদায়ও একাত্মতা প্রকাশ করেন। তারা জমিদার, মহাজন, দারোগা ও কোম্পানির দালালদের আক্রমণ করে; বহু জমিদার ও মহাজন নিহত হয়।
- এই বিদ্রোহে সিধু ও কানহু মুর্মু ছাড়াও চাঁদ, ভৈরব, বীর সিং, কালো প্রামাণিক, ডোমন মাঝি প্রমুখ সাঁওতাল নেতা সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেন।
- ইংরেজ সরকার প্রথমে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেও সাঁওতালরা তাতে কর্ণপাত করেনি। ফলে কোম্পানি প্রশাসন বিশাল সেনাবাহিনী ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দমন অভিযান চালায়। কামান ও বন্দুকের মুখে তীর-ধনুকধারী সাঁওতালরা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাস্ত হয়।
- ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়। সিধু, কানহুসহ বহু সাঁওতাল নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, শত শত বিদ্রোহীকে ৭ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কোম্পানি সৈন্যরা ৩৬টিরও বেশি সাঁওতাল গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।
সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব ও ফলাফল:
১৮৫৫–৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বিদ্রোহ ভারতের উপনিবেশিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।
প্রশাসনিক পরিবর্তন:
বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের বিষয়ে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়।
- সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলকে পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে “সাঁওতাল পরগনা জেলা” গঠন করা হয়।
- সাঁওতালদের পৃথক উপজাতি (Tribe) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- মহাজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং ঋণের সুদের হার বেঁধে দেওয়া হয়।
- সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা সাঁওতালদের অভিযোগ ও সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল হন।
ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব:
বিদ্রোহের পর ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা সাঁওতাল পরগনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। যদিও এতে সাঁওতাল সমাজে নতুন ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি হয়, তবুও তাদের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।
রাজনৈতিক প্রভাব:
এই বিদ্রোহ ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও প্রতিবাদের চেতনা সৃষ্টি করে। কৃষক, কারিগর, ও সাধারণ মানুষ প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়ায়।
ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় যথার্থই বলেছেন—
“এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছিল এবং ইহা ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত স্বরূপ।”
স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত:
অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহই ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—
“যদি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়, তবে সাঁওতালদের এই সংগ্রামকেও সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত।”
অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ মন্তব্য করেন—
“এই বিদ্রোহ ছিল সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধ।”
সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এটি ভারতীয় ইতিহাসে এক অমর অধ্যায়। এই বিদ্রোহ সাঁওতালসহ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা, ন্যায় ও আত্মমর্যাদার চেতনা জাগিয়ে তোলে। তাই একে যথার্থই ভারতের প্রথম কৃষক-আদিবাসী স্বাধীনতা আন্দোলন বলা যায়।
উপসংহার:
১৮৫৫–৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি কেবল সাঁওতালদের ক্ষোভ ও বঞ্চনার প্রকাশ নয়, বরং ছিল শোষণ, অন্যায় ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক মহত্ সংগ্রাম।
যদিও এই বিদ্রোহ ইংরেজদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল, তবু এটি ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার চেতনা প্রজ্বলিত করে।
সিধু-কানহু, চাঁদ, ভৈরব প্রমুখ সাঁওতাল নেতারা তাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণ করেন—
স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য লড়াই কখনও বৃথা যায় না।
পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
তাই সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধু একটি আদিবাসী আন্দোলন নয়, বরং ভারতের প্রথম কৃষক-জনতার মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক —
এক অমর সাহস, ঐক্য ও আত্মত্যাগের ইতিহাস।
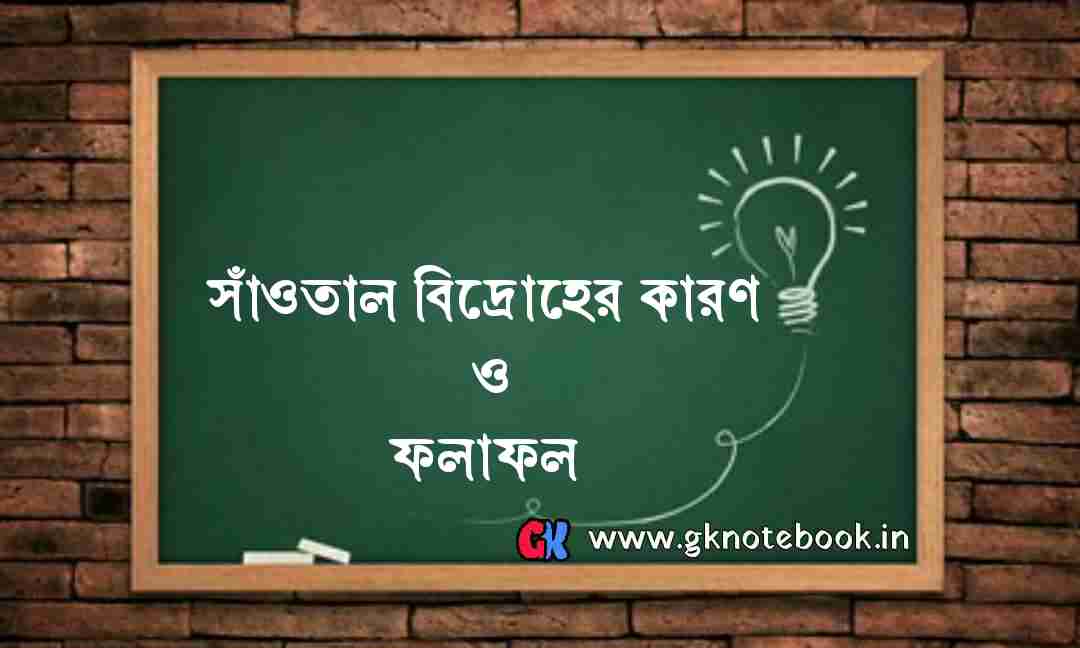
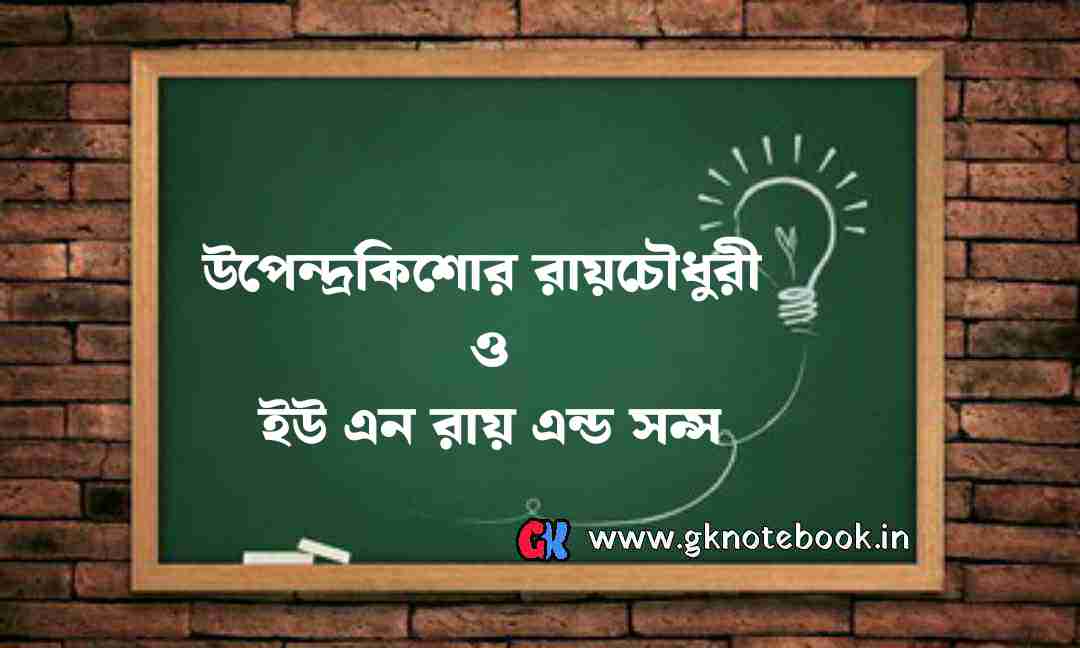
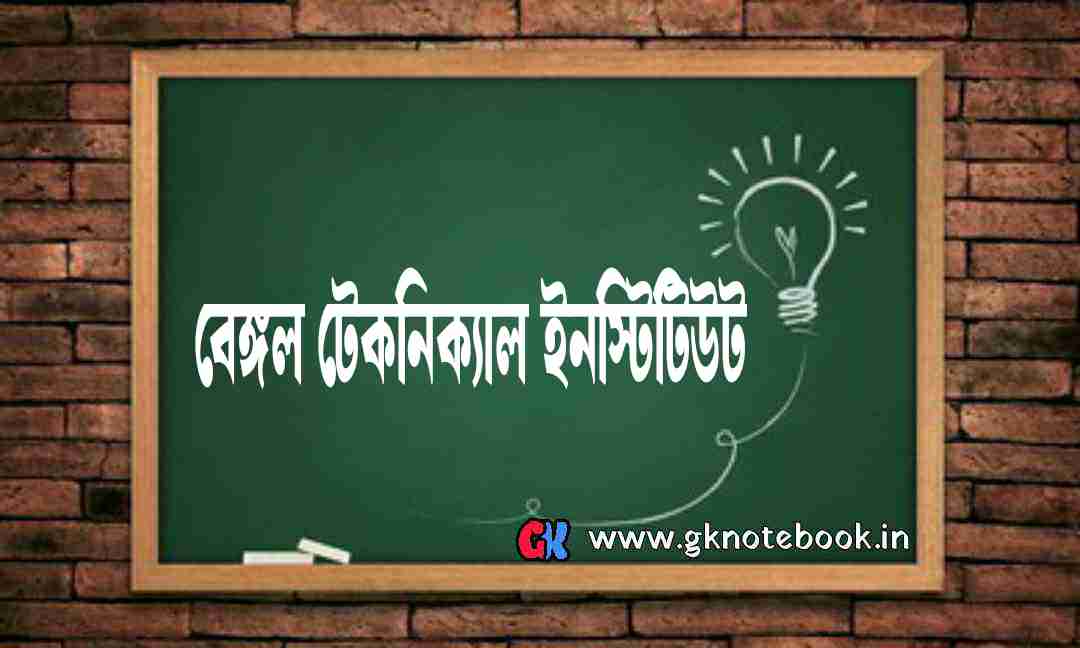
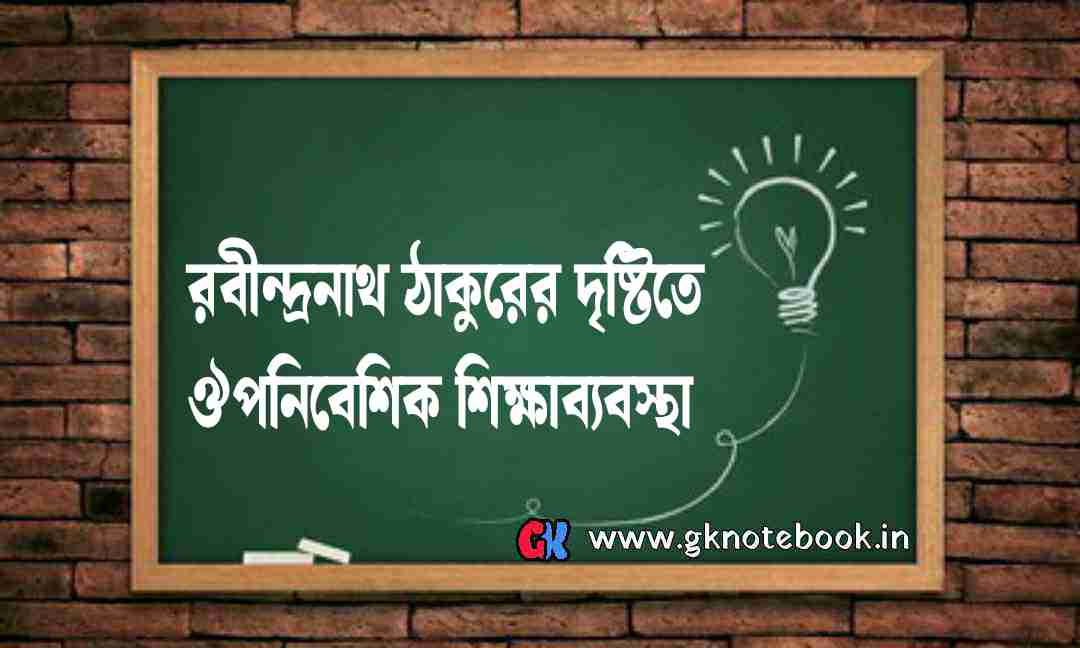
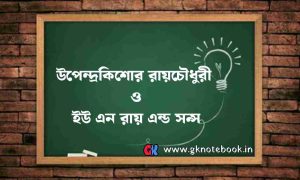
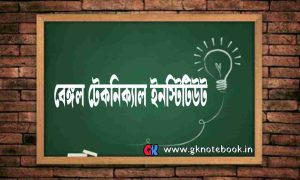
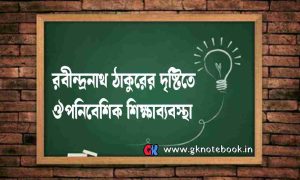
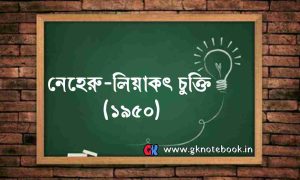
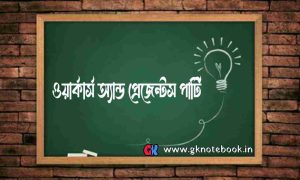
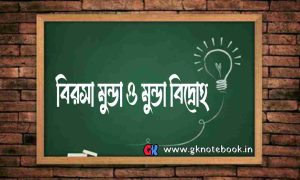

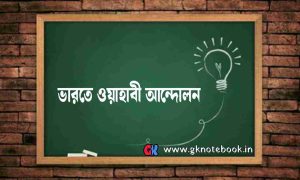
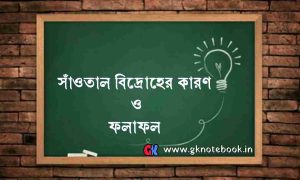
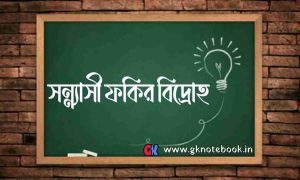
Post Comment